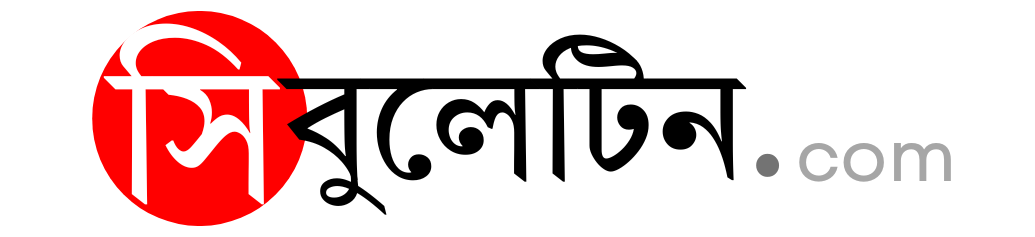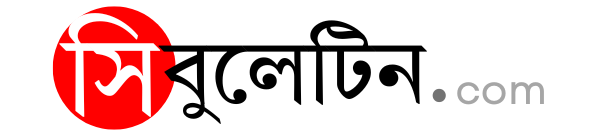পঁচিশে বৈশাখ ২০২৫: যে দেশ ফুটবল অনুরাগীদের কাছে গ্যব্রিয়েল বাতিস্তা, মারাদোনা আর মেসির জন্য প্রিয়, লাতিন আমেরিকার সেই দেশ আর্জেন্টিনা একদিন আপন করে নিয়েছিল আমাদের বিশ্বকবিকে। তার আগেই অবশ্য কবি পাড়ি দিয়েছিলেন আন্দিজ পর্বতমালার আড়ালে, সুদূর লিমা নগরীর উদ্দেশ্যে। এক অদ্ভুত শারীরিক দুর্বলতা ও হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভিনদেশে। রবীন্দ্রজীবনের এই অধ্যায়টি এক রোমাঞ্চকর, আবেগঘন ও ঐতিহাসিক ভ্রমণপত্র।
১৯২৪ সাল। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী তখন ছড়িয়ে পড়েছে কবিগুরুর কবিতা, দর্শন, শিল্প ও চিন্তাধারা। হঠাৎই পেরু সরকারের কাছ থেকে এল আমন্ত্রণপত্র। তাঁদের দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে কবিগুরুকে আমন্ত্রণ জানানো হল। উদ্দেশ্য ছিল, অনুষ্ঠানে এসে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেবেন এবং তাঁদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আন্তর্জাতিক মর্যাদা যোগ করবেন। বিশ্বকবিও সেই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। তেষট্টি বছর বয়সে মনের জোরে পাড়ি জমালেন লাতিন আমেরিকার উদ্দেশ্যে।
শুরু থেকেই এই যাত্রা কবির জীবনে নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। ভারত সাগর হয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের দীর্ঘ সমুদ্রপথে কবির শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল। বিপদ ঘনিয়ে এল তাঁর অসুস্থতা ঘিরে। জাহাজে থাকা অবস্থাতেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে বিশ্রাম নিতে থামতে হল পেরু পৌঁছনোর আগেই। কবির সহযাত্রী এবং সঙ্গী লেনার্ড এলমহার্স্ট অসুস্থ কবিকে নিয়ে উঠলেন আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে। শহরতলির প্লাজা নামক এক ছোট হোটেলে ঠাঁই হল তাঁর।
এখানেই পরিচয় হল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে। শুরু হল কবিজীবনের আর একটি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। নিজের শহরে প্রাণের কবির আসার খবর শুনে ঘরে থাকতে পারেননি ওকাম্পো। ছুটে গেলেন তিনি কবির কাছে। একপলক দেখবেন সেই গীতিকারকে যার কাব্য তাকে ঋদ্ধ করেছে, করেছে খাঁটি, দিয়েছে জীবনের সন্ধান। কবিকে দেখে কবির অসুস্থতায় তিনি উদ্বেলিত হলেন। কবিকে সুস্থ করার জন্য হোটেল থেকে একটি বাগানবাড়িতে নিয়ে এলেন তিনি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল কবির পেরু যাত্রা বাতিল। তবে সেই যাত্রা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক গন্তব্যে। কবির সেই অসম্পূর্ণ যাত্রাই অবশেষে লিখে গেল তাঁর জীবনে ভিন্ন এক ইতিহাস।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন আর্জেন্টিনার স্থানীয় এবং প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা। দান্তের ‘দ্যা ডিভাইন কমেডি’র হাত ধরে সাহিত্যের পরিমন্ডলে তাঁর অভিষেক ঘটে। রোম্যাঁ রোলাঁর লেখার মাধ্যমে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কবিগুরুর লেখা ও দর্শনের সঙ্গে। কবির লেখায় তিনি সুখ, দুঃখ ও ওপার প্রশান্তির ছোঁয়া পেতেন। অ্যান্দ্রে গিদের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের অনুবাদ পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ‘সুর’ পত্রিকার সম্পাদিকা। লাতিন আমেরিকার প্রায় সব কবি এবং লেখকদের লেখা প্রকাশ পেয়েছিল এই পত্রিকায়। ব্যক্তিত্বময়ী এই নারী আর্জেন্টিনার শাসক পেরণকে প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্য ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কারাবাসও পালন করেছিলেন।
ওকাম্পো কবিকে বুয়েনস এইরেসে শহরের নিকটে সান ইসিদ্রোতে তাঁর গ্রামের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। এই বাড়িই আজ ভিলা ওকাম্পো নামে পরিচিত। কিন্তু বাদ সাধলেন ওকাম্পোর বাবা-মা। ভিক্টোরিয়ার বাবা-মা কবিকে তাঁদের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। অগত্যা ঘর ভাড়া করতে হল ওকাম্পকে। নিজের বাড়ি থেকে অনতিদূরে শান্ত জনপদে ভাড়া নেওয়া হল একটি ভিলা। এই ভিলাকেই আমরা ‘মিরালোরিও’ নামে চিনি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু’মাস ওকাম্পোর আতিথ্যে এখানে ছিলেন। ১৯২৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত।
সান ইসিদ্রোর প্রাসাদসম এই বাংলো ছিল প্রকৃতির কোলে, প্লাটা নদীর ধারে, পাখির কলতানে ঘেরা। কবি এখানে পেয়েছিলেন এক অনাবিল শান্তি। ওকাম্পোর আতিথেয়তায় কবির অসুস্থতা কিছুটা কাটতেই তিনি আবার লিখতে শুরু করেন। ভিক্টোরিয়া আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে কবি কলম ধরেছিলেন। এখানে বসেই তিনি প্রায় তিরিশটি কবিতা লেখেন যার বেশিরভাগই ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য রচনার ‘বলাকা’ পর্বের একটি কালজয়ী সৃষ্টি হল ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে কবি ‘বিজয়া’ বলে ডাকতেন। আর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ‘পূরবী’ প্রকাশের সময় কবি ‘বিজয়া’ ওকাম্পোকেই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন।

ওকাম্পোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিছক আতিথেয়তার সম্পর্ক ছিল না। এটি ছিল আত্মার বন্ধন। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও হৃদয়ের মাঝে এক গভীর সংযোগ। ব্যক্তিত্বময়ী, সুসাহিত্যিক এবং মানবদরদী এই নারী রবীন্দ্রভাবনাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। কবির সৃষ্টিতে নিয়ে এসেছিল নতুন জোয়ার। ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে কবি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পরেও কবি ফেলে আসা সেই দিনগুলো বারবার স্মৃতিচারণা করতেন। চিঠির আদানপ্রদানে দুজনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল বটে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারতেন।
ওকাম্পো ছিল কবির অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সংশোধন করার জন্য যে আঁকিবুঁকি টানতেন, ওকাম্পের অনুপ্রেরণায় সেগুলি ফুটে উঠেছিল বড় ক্যানভাসে। ভিক্টোরিয়ার হাত ধরে কবি আবার রং-তুলির ক্যানভাসে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। এই উদ্যোগের কেন্দ্রে ছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এটাই ছিল দুজনের মধ্যে শেষ দেখা।
আর্জেন্টিনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের আন্তরিকতা এবং বিশেষ করে তাঁর প্রতি ওকাম্পোর প্রেম রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রাচ্য সভ্যতার পাশাপাশি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও রয়েছে সমৃদ্ধ আত্মা ও সংস্কৃতির স্পন্দন। তাঁর এই উপলব্ধি, সেই সময়কার ভারতের জন্য ছিল এক সাহসী উপলব্ধি, যেখানে উপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বকে দেখার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। আর বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল রবীন্দ্র সাহিত্যর এক মহান নারীচরিত্রকে।
আজ ২৫শে বৈশাখ, কবিগুরুর জন্মদিনে বিশ্বকবির প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।
লেখক: শিক্ষক ও লেখক

শিক্ষক ও লেখক